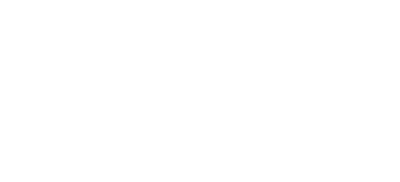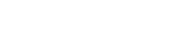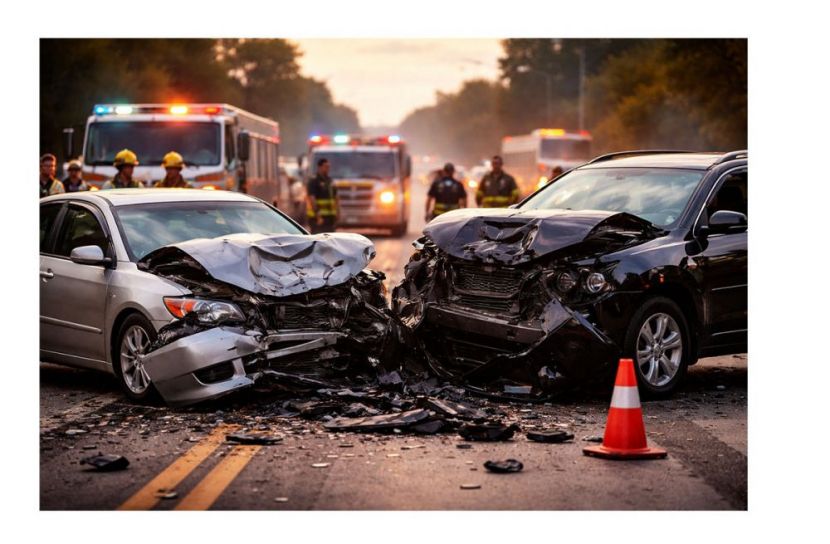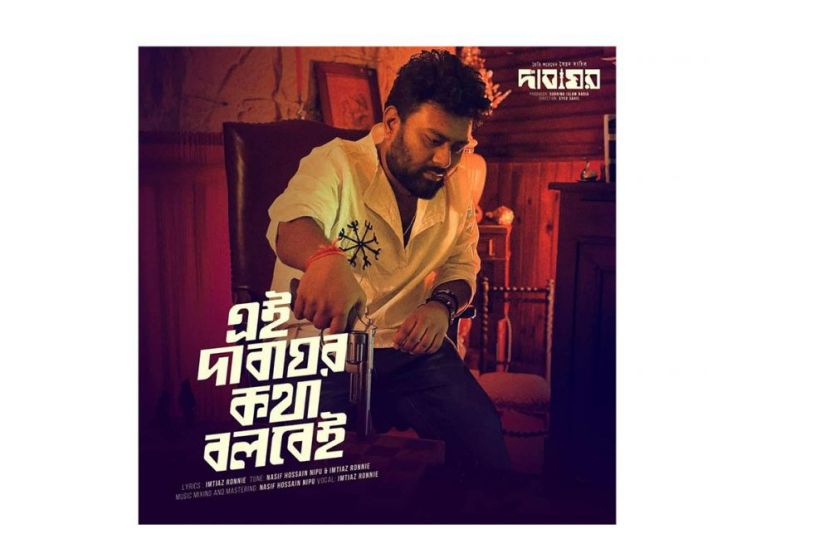২৩ জুলাই, ২০২৫। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক ও বীরত্বমূলক মুক্তিযুদ্ধের অধ্যায় ও তার নায়কদের নিয়ে যত কিছু লেখা হয়েছে, ওই তুলনায় দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে নিয়ে লেখালেখি হয়েছে যথেষ্ট কম। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখার (‘তাজউদ্দীন আহমদ: অনারিং দ্য মেমোরি অব এ হিরো অব আওয়ার লিবারেশন স্ট্রাগল’) শেষে তাই বলেছেন, “এমন একজন মানুষ আমাদের ইতিহাস চেতনার আড়ালে পড়ে আছেন, সেটাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অসম্পূর্ণতার কথা বলে।” (ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নাগরিক-এর তাজউদ্দীন আহমদ স্মারক সংখ্যা, ২০১৯) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় এই দৃশ্যমান ঘাটতির একটা ভালো দিক হচ্ছে, অন্যায্য সুবিধা বাগিয়ে নেয়ার সুযোগ না থাকায় তাকে নিয়ে বাজে বইও কম লেখা হয়েছে।
তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে লেখা ভালো বইগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশের একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসানের ইংরেজিতে লেখা ‘গ্লোরি অ্যান্ড ডিসপেয়ার: দ্য পলিটিক্স অব তাজউদ্দীন আহমদ’। বইটিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের ষাটের দশক থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী অর্ধদশক পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে ছোট ছোট অনেকগুলো প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন সময় ধারবাহিকভাবে নয়, বরং স্বতন্ত্র একেকটা লেখা হিসেবে তৈরি হওয়ায় এতে পুনরাবৃত্তি আছে অনেক। কিন্তু সৈয়দ বদরুল আহসানের সাহিত্যধর্মী হৃদয়গ্রাহী লেখার গুণে সেসব পাঠ ক্লান্তিকর না হয়ে, পাঠকের জন্য ইতিহাসবোধকে বারবার শক্তিশালী করার একটা উপায় হয়ে ওঠে। আর গৌরব ও হতাশার এই আবেগঘন রাজনৈতিক বয়ানের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন এক দূরদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত এবং বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতা ও অনমনীয় আদর্শে উজ্জ্বল এক মহান মানুষ ও নেতা— তাজউদ্দীন আহমদ। (২০০ পৃষ্ঠার এ বইটি ২০১৮ সালে প্রকাশ করেছে শ্রাবণ প্রকাশনী।)
তাজউদ্দীনের ছবি ভেসে ওঠে যিনি জাতির সংকটময় ও প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নেতৃত্বের হাল ধরতে দ্বিধা করেন না আবার অনৈক্য ও বিভেদের ফাঁদ থেকে দেশকে মুক্ত রাখবার জন্য তা ফেলে দিতেও কার্পণ্য করেন না। যার রাজনৈতিক জীবন গণমুক্তির স্বপ্নতাড়িত, একটি সশস্ত্র যুদ্ধকালীন সফল নেতৃত্বে উজ্জ্বল, অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর একটি রাষ্ট্র নির্মাণের সংগ্রামে আপসহীন— এমনসব উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে ব্যতিক্রমী ও আলোকিত।
সৈয়দ বদরুল আহসান তুলে এনেছেন ১৯৬৫-এর এক চন্দ্রিমা রাতে শীতলক্ষ্যা নদীতে ভাসমান নৌকায় সংঘটিত ওই নাটকীয় মুহূর্ত যখন বঙ্গবন্ধুর কাছে তরুণ তুখোড় অর্থনীতিবিদদের প্রস্তাবিত ছয় দফার নানাদিককে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাকে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করেছিলেন তাজউদ্দীন। ১৯৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ৬ দফা ঘোষণার পর পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন ঢাকার পল্টন ময়দানে ছয় দফা নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্কের। ওই চ্যালেঞ্জ আলিঙ্গন করেন তাজউদ্দীন আহমদ। কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে ভীত ভুট্টোকে আর পাওয়া গেল না ওই বিতর্কের মাঠে। আবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্যে ১৯৭১-এর মার্চে ইয়াহিয়া খানের পূর্ব পাকিস্তানে আসার মুহূর্তে, এই ভুট্টোই ইয়াহিয়াকে সতর্ক করেছিলেন কেবল একজন সম্পর্কে যাকে ভুট্টো সবসময় ভয় করতেন সবচেয়ে বিপজ্জনক হিসেবে— তিনি তাজউদ্দীন আহমদ।
১৯৭১ সালে যখন সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছত্রভঙ্গ তখন তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তার এই সাহসী বীরত্বমূলক নেতৃত্বের ভূমিকা তার কুচক্রী রাজনৈতিক সঙ্গীদের ঈর্ষান্বিত করে ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে মাঠে নামায়। খন্দকার মোশতাক ও শেখ মনিসহ এসব কুচক্রীর ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও কেবল অব্যাহতই থাকে না তা আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়ে ওঠে।
১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নিয়ে ‘মূলধারা ’৭১’ বইটিতে (ইউপিএল ১৯৮৬) মঈদুল হাসান লিখেছেন, ৫ ও ৬ জুলাই শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে তাজউদ্দীনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে অনেকেই দ্রুত ফল আশা করছিলেন ও ব্যর্থতার অভিযোগ তুলছিলেন। এ অনুষ্ঠানে তাজউদ্দীন ঘোষণা করেন: বিজয়ের জন্য যে দীর্ঘ সংগ্রাম ও অশেষ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, তা সকল প্রতিনিধির পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, ফলে যোগ্যতর নেতৃত্বের উদ্ভব সেখানে ঘটবেই; তিনি নিজেও যদি সক্ষম না হন, তবে যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ তাকে ছেড়ে দিতে হবে; কিন্তু বিজয় বাংলাদেশের অনিবার্য।
সৈয়দ বদরুল আহসান লিখেছেন, “তাজউদ্দীন ছিলেন অবিচলিত যিনি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে চললেন। তার ভিতরকার সমাজতান্ত্রিক মানুষটি ষড়যন্ত্রীদের কাছে মাথা নোয়ায়নি। তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সঙ্গী আওয়ামী লীগারদের ছুঁড়ে দেয়া আক্রমণ মোকাবিলা করেছে। ঐ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন একজন ব্যথিত তবে আরও শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান হয়ে।”
কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দীন হলেন অবহেলিত। তার সরকারের আকস্মিক ছেদ ঘটল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারে তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। বদরুল লিখেছেন, “তিনি অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে অসাধারণ সাহসিকতা দেখিয়েছেন। এই অশুভ শক্তি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও স্থানীয় সুযোগসন্ধানীদের রূপে ও আকৃতিতে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে কোনো বিদেশি সাহায্যের দরকার নেই, বিশেষ করে সেইসব দেশ থেকে যারা এর জন্মের বিরোধিতা করেছে। তার এই অবস্থান সরকারের ভিতরকার ডানপন্থী শক্তির কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। এইসব লোক শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে লাগাতার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে চলেছে।”
কুচক্রীদের চেষ্টা সফল হলো। তাজউদ্দীনের কাছে বঙ্গবন্ধুর নোট এলো যাতে তাকে বলা হলো মন্ত্রীপরিষদ থেকে অব্যাহতিপত্র জমা দিতে। যেমন চাওয়া হলো তাজউদ্দীন তাই করলেন। “এটি ছিল ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাস— সেই মাস যখন ১৯৭১-এ বাঙালি নিধনে পাকিস্তানকে পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী নিক্সোনিয়ান নীতির স্থপতি হেনরি কিসিঞ্জার বাংলদেশে এলেন। কিসিঞ্জারের এই ভ্রমণ হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য মার্কিন কক্ষপথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি প্রতীক। দেশ ঢুকলো মার্কিন কক্ষপথে। তাজউদ্দীন আহমদের সমাজতন্ত্র অপসারিত হলো লাগামহীন পুঁজিবাদ ও আঁধারের লুণ্ঠকদের উত্থানে। সেই অক্টোবর থেকে বাড়তে বাড়তে এই লুণ্ঠকদের সংখ্যা এখন বহুগুণে পৌঁছেছে।”
বইয়ের ইমেজ অব সেলফইফেসমেন্ট অধ্যায়ে লেখক বদরুল এ কথাগুলো বলেছেন। একইসঙ্গে দেখিয়েছেন একজন জননেতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য যিনি তার আত্মস্বার্থ মিলিয়েছেন গণস্বার্থের সঙ্গে, আত্মপরিচয় দাঁড় করিয়েছেন বাঙালির স্বাধীন জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার ওপর, পরিবারের ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে একাত্তরের যুদ্ধময় দিনগুলোতে জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন, আর তারপর কোনো বিভেদ তৈরি না করে চুপচাপ সরে গেছেন সরকারের ক্ষমতাবলয় থেকে। বদরুলের ভাষায় (ইংরেজিতে), “১৯৭৪ সালের অক্টোবর থেকে পরের বছর নভেম্বরে তার খুন হওয়া পর্যন্ত তিনি একরকম নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন। তিনি বেদনাকে আলিঙ্গন করেছেন ও যে দেশকে স্বাধীনতার বন্দরে পৌঁছে দিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে একাকী চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন। সবশেষে দিয়েছেন উচ্চমূল্য।”
তাজউদ্দীন মনেপ্রাণে ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রী, তবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের খপ্পর থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে মুক্ত করে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা ছিল তার লক্ষ্য। তবে এই সমাজতন্ত্র অর্জন করতে জনগণকে শ্রম ও সাধনা করতে হয়। হঠাৎ কোনো সরকারি ঘোষণা দিয়ে প্রকৃত সমাজতন্ত্র হয় না। অনেকে মাথা নোয়ালেও আমৃত্যু গণতন্ত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাজউদ্দীন তাই বাকশালের একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেননি।
বইয়ের শেষ অধ্যায়ে সৈয়দ বদরুল আহসান লিখেছেন, তাজউদ্দীন ক্ষমতাবানদের সামনে দাঁড়িয়েও তার আদর্শ বিসর্জন দেননি। ১৯৭২-এ তিনি বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সঙ্গে দেখাই করেননি। কিন্তু ১৯৭৪-এ পরিস্থিতি পালটে গেছে। তবে সেসময়ও ওয়াশিংটনে দুজন যখন আলোচনায় বসেন, বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে কীভাবে সহায্য করতে পারে, ম্যাকনামারার এ প্রশ্নে তাজউদ্দীনের স্পষ্ট জবাব: মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশে কৃষকদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে— তাদের হালের বলদ মারা গেছে, অনেকের গরু বাঁধার দড়িও নেই। অতএব বাংলাদেশের কৃষকদের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, গরু, টিনের গোয়াল ঘর ও দড়ি। যেহেতু বিশ্ব ব্যাংক এসব দেয় না, তাদের কাছ থেকে সাহায্যেরও কোনো প্রয়োজন নেই।
এমন স্বাধীন ও সাহসী ভূমিকাই জনগণ রাষ্ট্রনেতাদের কাছ থেকে আশা করে। কিন্তু এমন রাষ্ট্রনেতা বছরে বছরে আসে না। আগামীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলো মোকাবিলা করার জন্য তাজউদ্দীন পাঠ ও চর্চা তাই স্বাভাবিকভাবেই দিনে দিনে বেশি করে জরুরি হয়ে পড়ছে।